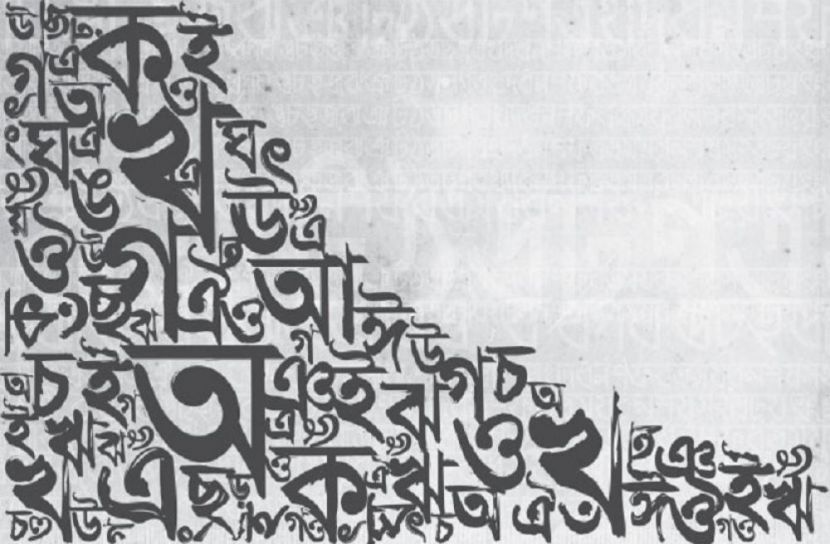
~সন্দীপন সান্যাল
বাংলা ভাষার বয়স কত? নানা মুনির নানা মত। ডক্টর মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ এর মতে শপ্তম শতকে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয় প্রাকৃত বাংলা ভাষা। তবে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতবাদই বেশী প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করেন ৯৫০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মাগধী অপভ্রংশ থেকে এসেছে কোমল মধুর আ-মরি বাংলা ভাষা।
পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী বাংলা ভাষা ও এর সাহিত্যকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যেতে পারে।
আদিযুগ – ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ। নেপালের রাজসভায় আবিষ্কৃত “চর্যাপদ” এ যুগে রচিত।
ক্রান্তিযুগ – ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ। এ সময়ের বাংলা ভাষার কোন নমুনা পাওয়া যায় না।
মধ্যযুগ – ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ। এ সময় বাংলা ভাষার লেখা সাহিত্য অনায়াসে পড়া যায় ও বোঝা যায়।
আধুনিক যুগ – ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমান। বহু নদী সরোবর পেড়িয়ে আজকের এই রূপ।
নীচে এই চারটি যুগের কিছু কথা লিখি।
আদিযুগঃ
১৯০৭ অব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালায় আবিষ্কার করেন এ যুগের চারটি পুঁথি। চরজ্যাচরজ্যবিনিশ্চয়, দেহাকোষ – ১, দেহাকোষ – ২ ও ডাকার্ণব। এ গুলো পরবর্তীতে চর্যাপদ নামে পরিচিত হয়। এতে আছে ২৪ জন বৌদ্ধ বাউলের লেখা ৪৬ টি পূর্ণ ও ১টি খন্ডিত গান। “চর্যা” শব্দের অর্থ ‘আচরণ’। এতে নানা গানে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা ধর্মের গূঢ় কথা বলেছেন – তাই এঁকে তান্ত্রিক গাঁথাও বলা যেতে পারে।
এখানে আদি ভাষায় রচিত কয়েকটি বাক্য আর তার পাশাপাশি বর্তমান রূপ উল্লেখ করা হ’ল।
‘গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ’ – গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা চলে।
‘সনে ভরিলী করুনা নাবী’ – সোনায় ভরা আমার করুনা নৌকা।
‘নিসি অন্ধারি মূসার চারা’ – অন্ধকার রাত, ইঁদুর চড়ছে।
এ ভাষাকে ‘সন্ধ্যাভাষা’ ও বলা হয় – মানে আলো আঁধারি, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বোঝা যায় খানিক বোঝা যায় না।
ক্রান্তিযুগঃ
পুরো দেড়শ বছরের এ কালটি যেন পুরো হারিয়ে গেছে। এ সময় কি বাংলা ভাষা ছিল না? আগে আছে, পরে আছে, মাঝে এ ফাঁক ভাষাবিদদের ঝামেলায় ফেলে। মধ্যযুগের প্রথম আবিষ্কৃত “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” যেন এক দূরের সম্পর্ক তৈরি করেছে চর্যাপদের সাথে। পরিবর্তনের সোপানগুলো অজানা রয়েছে। লক্ষণ সেনের পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্য যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়।
মধ্যযুগঃ
বসন্ত রঞ্জন রায় আবিষ্কার করলেন বাংলা ভাষার মধ্য যুগের সূচনাকালের রূপ “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” – মহাকবি বডু চন্ডিদাস (বাংলা সাহিত্যের প্রথম রবীন্দ্রনাথ) –এর মহাকাব্য। এ যেন যমুনার কলতান –
“আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শব দেঁ মোর আউলায়লোঁ রান্ধন।।”
মধ্যযুগের প্রথম প্রদীপ “মঙ্গলকাব্য”। এর কাহিনী সাধারণ মানুষের নয়, দেবতাদের। অধিকাংশ কাব্যে রয়েছে স্বর্গের কোন শাপ গ্রস্ত দেবতার মর্ত্যে সাধারণ মানুষ হয়ে বিচরণের পাঁচালী। কাব্যগুলোর নাম হোত দেবতাদের নামানুসারে। যেমন, হরি মুকুন্দ রায় ও ভারত চন্দ্রের “চন্ডীমঙ্গল্কাব্য”, বিপ্রদাসের “মনসামঙ্গলকাব্য” বা “শিবমঙ্গলকাব্য”। একই বিষয়, তাই কালে কালে এগুলো হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর। কোন মৌলিকতার ছাপ ছিল না।
মঙ্গলকাব্য ছন্দে রচিত। কোন কোন কাহিনী এখন ঘরে ঘরে ফেরে – যেমন বেহুলা – লখিন্দর। মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য ধর্ম ভিত্তিক, দেবতা কেন্দ্রিক। দেবতার কথার ফাঁকে ফাঁকে এসেছে মানুষ।
চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে এল দখিনা বাতাস। রাধা ও কৃষ্ণ এর নায়ক-নায়িকা। সুবেদার আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ্ এর আমলে চৈতন্যদেব নিয়ে এলেন বৈষ্ণব দর্শন। এ কালের চার মহাকবি বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। বৈষ্ণব কবিতা ছোট খাটো – রয়েছে রাধা কৃষ্ণের প্রেম ও বিরহ, হৃদয়ই এখানে মূল উপজীব্য। এখানে পাওয়া যায় মানুষের দুঃখ ও আনন্দের সারসত্তা।
‘সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ’
বিদ্যাপতি কবিতা রচনা করতেন ‘ব্রজবুলি’ ভাষায় – মিষ্টি, সুরময়, গীতিময় ভাষা। এ ভাষায় কঠিন শব্দকে ভেঙ্গে সহজ করা হয় – যেমন বিদ্যুত কে বিজুরি। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় এ ভাষার প্রেমে পড়েছিলেন।
‘যব – গোধুলি সময় বেলি।
ধনি – মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা।’ – বিদ্যাপতি
মধ্যযুগের আরেক অবদান অনুবাদ সাহিত্য। সেকালের মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণত হিন্দু কবিরা অনুবাদ করতেন। কৃত্তিবাস রামায়ন এবং কাশীরাম মহাভারত অনুবাদ করে পরবর্তীতে প্রায় দেবতার মর্যাদা লাভ করেন।
পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমান কবিরা বাংলা কবিতায় হাত দেন। এরা মুলতঃ এ এলাকারই –ধর্মান্তরিত। বাংলা ভাষার প্রথম মুসলমান কবি শাহ্ মুহাম্মদ সগীর। প্রথম কাব্য “ইউসুফ-জুলেখা”। এবার কাব্যে এলো নতুন বিষয়, লাইলি-মজনুর কেচ্ছা। আর কাব্য ইতিহাস। তবে সবই মুলতঃ ফারসি, আরবি ও হিন্দি থেকে অনূদিত। ষোড়শ শতকের শেষভাগের কয়েকটি বিখ্যাত রচনা আফজল আলীর “নসিহৎনামা”, জৈনুদ্দিনের “রসুল বিজয়”, শেখ ফজলুল্লাহ’র “গাজী বিজয়”। এর পরে সপ্তদশ শতকে আরাকান বা রোসাঙ্গ দরবারে প্রকাশ পেল আরো কিছু বিস্ময়কর প্রতিভা। এলেন মধ্যযুগের মুসলমান কবি শ্রেষ্ঠ আলাওল। তার শ্রেষ্ঠ রচনা “পদ্মাবতী” হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সির “পদুমাবত” – এর কাব্যানুবাদ। এ সময়ের আরো দুটি বিখ্যাত রচনা দৌলত গাজীর “সতী ময়না” এবং মাগন ঠাকুরের “চন্দ্রাবতী”।
মধ্যযুগ থেকে হিন্দু ও মুসলমান একসাথে বুনে যেতে থাকে বাংলা ভাষায় কাব্যলক্ষীর শাড়ীর পাড়।
আধুনিক যুগঃ
উনিশ শতকে সূচিত হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকতার যুগ, এর প্রতিটি শাখা সম্পূর্ণতা পায়। এ সময়ের প্রথম সূর্য বাংলা গদ্য। ফোর্ট উইলিয়ামের কলেজের লেখকেরা নিয়ে এলেন এক নতুন অধ্যায়। প্রথম গদ্য গ্রন্থ রাজরাম বসুর “প্রতাপাদিত্য চরিত্র” প্রকাশিত হয় ১৮০১ অব্দে। বিদ্যালঙ্কার লিখলেন বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি ও প্রবোধচন্দ্রিকা। লিখলেন গোলনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রামকিশোর তরকালঙ্কার, হরপ্রসাদ রায় ও আরো অনেকে। রামমোহন রায় গদ্যকে পাঠ্য বইয়ের বৃত্ত থেকে বিস্তৃততর এলাকায় নিয়ে যান। সাহিত্যে নতুন তারা খচিত হলেও গদ্য তখন নাবালক, ছিল না দাড়ি, কমা বা অন্য কোন যতি চিহ্ন।
যাঁর হাতের ছোঁয়ায় বাংলা গদ্য রূপময় হয়ে ওঠে, তিনি বাংলা গদ্যের জনক ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর – সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের একজন। এনো যতিচিহ্ন। গদ্য যেন ফিরে পেল ছন্দ। বিদ্যাসাগরের প্রথম বই “বেতাল পঞ্চবিংশতি” বের হয় ১৮৪৭ অব্দে। তখনও গদ্য কেবল সাধু ভাষায় রচিত। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখলেন “আলালের ঘরে দুলাল”, অনেক ত্রুটি সত্যেও বাংলা সাহিত্যে কথ্য সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস। চলতি গদ্যের পথ বেয়ে আসেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তার “হুতুম পেঁচার নকশা” নিয়ে ১৮৬২ তে।
বঙ্কিম চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক, প্রথম রচনা “দুর্গেশ নন্দিনী”। বঙ্কিমের গল্পগুলো সম সামিয়িক কালের সাধারণ মানুষের গল্প নয়, ইতিহাস আর কল্পনা মিশিয়ে কাহিনী। সমকালীন অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর কয়েকটি হ’ল মীর মোশাররফ হোসেনের “বিশাদ সিন্ধু”, তারকানাথের “স্বর্ণলতা”, রমেশ চন্দ্রের “মাধবীকঙ্কন”।
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গদ্য রাজত্বে একমাত্র কবি ইশ্বর গুপ্ত। তাঁর কবিতা ব্যাঙ্গ বিদ্রুপে ভরা। এক ইংরেজ রমণীর উদ্দেশ্যে লেখা কবিতার দুটি চরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।
“বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে”
বাংলা কবিতায় আধুনিকতা আনেন কবি মধুসূদন দত্ত। রবীন্দ্রনাথের আগে তিনিই বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিভাবান কবি। তাঁর অন্যতম কীর্তি “মেঘনাদ বধ” মহাকাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, বাংলা সাহিত্যের শেষ সার্থক মহাকাব্য। এর ও পরে এল হেমচন্দ্রের “বীরবাহু”, কায়কোবাদের “মহাশ্মশান” – কিন্তু কোনটিই কালকে অতিক্রম করতে পারে নি। মধুসূদন মুক্তি দেন বাংলা ছন্দকে; পয়ার করে তোলেন প্রবহমান। তিনি লিখলেন সনেট যা বাংলায় “চতুর্দশপদী কবিতা” নামে পরিচিত।
বাংলায় প্রথম মৌলিক নাটক তারাচরন শিকদারের কমেডি “ভদ্রার্জুন” প্রকাশ পায় ১৮৫২ তে। তবে প্রথম সার্থক আধুনিক নাটক এসেছে মধুসুদনের হাত ধরে – শর্মিষ্ঠা। তিনি যেন একাই বাংলা সাহিত্যকে ৫০০ বছর এগিয়ে নিয়েছেন। একে একে রচনা করলেন “একেই বলে সভ্যতা”, “বুড়ো শালিকের ঘারে রোঁ”, “পদ্মাবতী” ও “কৃষ্ণকুমারী”। স্বল্পায়ু দীনবন্ধু মিত্রের “নীল দর্পণ” যেন বাংলার আকাশে “আঙ্কল টমস কেবিন”। উনবিংশ শতকের শেষাংশে আরো কয়েকজন স্বনামধন্য নাট্যকার হলেন জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ও ক্ষিরোধ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
বঙ্কিম –মধুসূদন পরবর্তীকালে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আকাশে প্রতিদিনের সূর্য, শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তিনি বিশ্বকবি। সাহিত্যের সকল শাখাতে অবাধ বিচরণ পৃথিবীতে খুব একটা নেই। ১৯১৩ সালে তাঁর ইংরেজিতে অনূদিত কাব্যগুচ্ছ “গীতাঞ্জলী” নোবেল পুরস্কার পায় – ভারত উপমহাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বাংলা বিশ্ব দরবারে স্থান করে নেয়। ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস ও সাহিত্যের অন্য শাখায় যে বিশাল পৃথিবী তিনি রচেছেন তাঢ় বর্ণনা এই স্বল্প পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়।
বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশক অনেক তরুন কবি এলেন, কিন্তু এদের সবাই ছিলেন মুলতঃ রবীন্দ্রনুসারী। এলেন ছন্দের জাদুলর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্র মোহন বাগচী। রবীন্দ্র জোয়ার থেকে বেড়িয়ে এসে সত্যিকারের নতুন ধারা যারা নিয়ে এলেন তাদের মধ্যে প্রথম সারির কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
নজরুল সাহিত্যের আকাশে ধুমকেতু, আসলেন, দেখলেন, মুহূর্তে জয় করে নিলেন সবকিছু। তিনি “বিদ্রোহী কবি” হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্যের মূলে প্রেমের প্রাধান্যই বেশী। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ “অগ্নিবীণা”, “বিষের বাঁশী”, “দোলন চাঁপা”, “ছায়ানট”। বাংলার আরেক ভিন্ন স্বাদের কবি পল্লী কবি জসীম উদ্দিন। পল্লীর জীবন ও কিংবদন্তি তাঁর কাব্যের অবলম্বন।
বিশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি আধুনিক কবিতা তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করে। এবার কবিরা তাদের আবেগকে শোধিত করেন মননশীলতা দিয়ে। যে পাঁচজন কবি আধুনিকতার আকাশ তৈরি করলেন তারা হলেন জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী। প্রতিভার বিচিত্রমুখিতায় বুদ্ধদেব বসু যেন আধুনিক রবীন্দ্রনাথ। তবে নির্জনতার কবি জীবনানন্দই পরবর্তীতে আধুনিক কবিতার জনক হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা “বনলতা সেন”, “ঝরা পালক” ও “রুপসী বাংলা”।
বিশ শতকের কথা সাহিত্য, গল্প ও উপন্যাস জীবনধর্মী। এ সময়ের অন্যতম দিকপাল কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। তাঁর কয়েকটি প্রধান উপন্যাস দেবদাস, পল্লী সমাজ, শ্রীকান্ত ও চরিত্রহীন। দেবদাস চরিত্র টি মজনু বা ফরহাদের মতই এক বিরহী প্রেমিকের প্রতীকে পরিণত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে এমন উদাহরণ খুব একটি নেই। ঔপন্যাসিক বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় পল্লী বাংলার গদ্য-মহাকাব্য রচয়িতা। “পথের পাঁচালি” তাঁর এক অমর সৃষ্টি।
অনেকের মতে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ আধুনিক ঔপন্যাসিক। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে কবি, গনদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা। এ সময়ের সারা জাগানো আরো কয়েকজন ঔপন্যাসিক হলেন মানিক বন্দোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু।
ছোট গল্প সম্পর্কে কিছু না বললে সাহিত্যের এক বিশাল শাখা অবহেলিত থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ই বাংলা ভাষায় ছোট গল্পের স্থপতি। উনিশ বিশ শতকে প্রাণ ভরে গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, যা পরবর্তীতে “গল্পগুচ্ছ” এর তিনটি খন্ডে সংগৃহীত হয়। এর পরে আসেন শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ এবং আরো অনেকে। এলেন চলতি রীতির প্রথম প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরী।
পূর্বসূরিদের সাজানো বাগান ধরে বিশ শতকের শেষ অংশে এপার বাংলা ওপার বাংলায় এলেন অনেক কবি, অনেক লেখক ও প্রাবন্ধিক। কালে কালে তাদের অপূর্ব সৃষ্টিতে বাংলা তার সুষমা ছড়িয়ে দেয় দেশ থেকে দেশান্তরে।
সূত্রঃ
১) লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনি – হুমায়ূন আজাদ
২) কত নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনি – হুমায়ূন আজাদ
৩) বাঙ্গালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তনধারা – আহমদ শরীফ
৪) বাঙ্গালীর ইতিহাস – নীহার রঞ্জন রায়
৫) বাংলা সাহিত্যের কথা – মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – সুকুমার সেন

